দেশের করব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার কার্যক্রমের পদক্ষেপ হিসেবে নতুন মূসক (ভ্যাট) আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
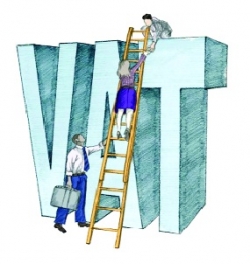
এ-সংক্রান্ত সরকারি ঘোষণা ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটেই ছিল। এতে আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কার— দুটি বিষয়ে দেয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। আইনগত সংস্কারের অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি পর্যালোচনা করে অনুধাবন করে যে, মূসক আইনে সংস্কার আনতে হলে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে এটি। এ কার্যক্রমের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আইনের খসড়া দাঁড় করানো হয়েছে এখন। বিদেশী অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের পাশাপাশি দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের সহায়তায় এ নতুন আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে। খসড়া আইনটি ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত করা হয়— জনগণের মতামত যাচাইয়ের লক্ষ্যে। একই সঙ্গে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে পুরনো ভ্যাট আইনে কিছু সংস্কারও আনা হয়। যে পরিবর্তন করা হয়েছে, তা নতুন আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর উদ্দেশ্য ছিল খসড়া আইন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হলে তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে যেন সমস্যা না হয়, সে লক্ষ্যে কিছুটা এগিয়ে থাকা। দেড় বছরেরও বেশি সময় ব্যয় করে দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এ খসড়া আইনের বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণই সম্পন্ন হয়েছে।
এরই মধ্যে মূসক কার্যক্রমের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত অর্থাৎ যারা এ আইনের মাধ্যমে প্রভাবিত হবেন বা কর প্রদানকারী (স্টেকহোল্ডার), ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি; তাদের অধিকাংশের সঙ্গে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় এফবিসিসিআই, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ঢাকা চেম্বার, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সসহ অনেক ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিনিধি যেমন হাউজিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিপ বিল্ডার্স, টেক্সটাইলসহ অধিকাংশ শিল্প ও ব্যবসায়িক খাতের প্রতিনিধি সংগঠনের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় সংসদের অর্থমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সঙ্গেও একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল নতুন আইন সম্পর্কে তাদের অবহিত করা, তাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে, সেগুলো গ্রহণ করা এবং তাদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে, সেগুলোর মূল্যায়ন ও প্রতিফলন ঘটানো। এসব কার্যক্রম বা পদক্ষেপ সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মনে করছে, আইনগতভাবে খসড়া ভ্যাট আইনটি পাস হওয়া দরকার। সঙ্গত কারণেই এটি মন্ত্রিপরিষদে পাঠানো হয়েছে এবং সম্প্রতি সেটি সংসদে উত্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনও দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সংসদ সদস্যদের ভোটে খসড়া আইনটি পাস হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আগামী বাজেট অধিবেশনে নতুন ভ্যাট আইনের সংসদীয় অনুমোদন হওয়াটাই কাম্য। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরেই এটি সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের কথা ছিল। এদিক থেকে সরকার একটু পিছিয়ে গেছে বলা চলে। তবে এ সময়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেক পরিবর্তনও আনা হয়েছে আইনে। এখন খসড়া আইনটি অনেক সমৃদ্ধ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সময় নষ্ট হয়েছে, তা বলা যাবে না। এতে খসড়াটি আরও পরিশীলিত ও মার্জিত হয়েছে। খসড়া হিসেবে আইনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় এটা করদাতাদের জন্য বিশেষভাবে সহায়কও বটে। সংসদীয় অনুমোদন হলে এটি আইনগতভাবে গৃহীত হবে আগামী অর্থবছরের শুরু থেকেই। কিন্তু বাস্তবায়ন হবে তিন বছর পর। এ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আইন বাস্তবায়নে যে প্রশাসনিক সংস্কার দরকার, সেটি করা হবে। আইন এবং প্রশাসনিক সংস্কারকে রেলগাড়ির ইঞ্জিন ও রেললাইনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রেললাইন ভালো না হলে যেমন ভালো ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেনের গতি বাড়ানো সম্ভব নয়, তেমনই প্রশাসনিক সংস্কার ছাড়া শুধু আধুনিক আইনের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের স্থায়ী প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়।
কর প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর আইনগত বিধান নতুন আইনের মাধ্যমে দেয়া হবে। এ জন্য আইনটি দ্রুত পাস করা দরকার। নইলে প্রশাসনিক সংস্কার বাধাগ্রস্ত হবে। অনেকে বলছেন, আইনটি তিন বছর পর যখন বাস্তবায়ন হবে, তখন কেন এত আগে পাস করা হচ্ছে। বিষয়টি আমাদের ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। তিন বছর পর আইনটি পাস হলে তা বাস্তবায়ন করতে লাগবে আরও তিন বছর। এতে করব্যবস্থার আধুনিকায়ন পিছিয়ে যাবে অনেক দিনের জন্য। এটি কারোরই কাম্য নয়।
আইনটি পাস হলে এর ছত্রছায়ায় প্রথম পদক্ষেপ হবে প্রশাসনিক সংস্কার। এ লক্ষ্যে এনবিআর রূপরেখা প্রণয়ন করেছে এরই মধ্যে, যা চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার সময় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। রূপরেখাটি এনবিআরের ওয়েবসাইটেও দেয়া হয়েছে। রূপরেখা হওয়া সত্ত্বেও প্রায় সব প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হয়েছে এতে। সরকারের জন্য বড় কাজ হবে, এ বিষয়গুলোকে বিস্তৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা। এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সরকার উভয়ের জন্যই একটি বড় পরীক্ষা। আইনটি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে তা দেশের করব্যবস্থায় বড় রকম পরিবর্তন আনবে। তবে সরকারকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে এটি। বাধা আসবে। সরকারের ভেতর থেকে রাজনৈতিক বাধা আসবে; রাজস্ব কর্মকর্তা, করদাতাদের থেকেও আসবে বাধা। পরিবর্তন অনেকেই চান না। কারণ পরিবর্তন মানে নতুনভাবে কিছু করা। যদিও আমরা জানি নতুনব্যবস্থায় একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে করদাতারা আর পুরনো আইনের দিকে ফিরেও তাকাবে না, তবু একটা ভয় থাকে। এ ভয় দূর করার দায়িত্ব সরকারের। ভয় ও প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে নতুন আইনকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর বিকল্প নেই।
খসড়া ভ্যাট আইনে করদাতাদের জন্য অনেক ভালো দিক আছে। যেমন বিদ্যমান আইনে সব ধরনের উপাদানের ওপর প্রদেয় ভ্যাট ক্রেডিট হিসেবে ফেরত পাওয়া যায় না। যেকোনো জিনিস উদ্যোক্তারা উপাদান হিসেবে ব্যবহার করবেন, পণ্য তৈরি ও সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সেটার সুবিধা তারা পাবেন নতুন আইনে। বর্তমান ব্যবস্থায় চলতি হিসাবব্যবস্থা বলবৎ আছে। পণ্য কারখানা থেকে বের হওয়ার আগেই ভ্যাট দিতে হবে। এটি ভ্যাট আইনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ। অথচ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কর দিতে হয় ক্রেতার নিকট পণ্যের সরবরাহ হওয়ার পর। খসড়া আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে এ ক্ষেত্রে। মাসে একবার ভ্যাট রিটার্ন জমা দেবেন করদাতা এবং একই সঙ্গে সব পণ্য সেবার ওপর প্রদেয় ভ্যাট পরিশোধ করবেন। প্রতিদিন ব্যাংকে গিয়ে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ভ্যাট পরিশোধ করার আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। বর্তমানে অনেক উদ্যোক্তা হয়রানি এড়ানোর জন্য কিছু অর্থ আগাম জমা দিয়ে রাখেন ভ্যাট প্রদানের জন্য। এটা তাদের জন্য ব্যয়সাপেক্ষ এবং এর বিলুপ্তি করদাতাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। মাসে এক পাতার ভ্যাট রিটার্ন জমা দিলেই হবে ভ্রমণ। ব্যাংকের মাধ্যমেও কর জমা দিতে পারবেন করদাতারা। কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে কর প্রদানের ক্ষেত্রে। এরই মধ্যে ‘বি ক্যাশ’সহ কর প্রদানের নানা পদ্ধতি চালু করার সম্ভাবনা পর্যালোচনা হচ্ছে। আধুনিক কর প্রদানব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হলে ব্যাংক থেকে অটোমেটিক ব্যবস্থায় পেমেন্ট করতে পারবেন উদ্যোক্তারা। নতুন আইন বাস্তবায়িত হলে ট্রেজারি চালান প্রথা বাতিল পর্যায়ে চলে যাবে। এটি পুরনো প্রক্রিয়া। এতে সময় নষ্ট হয়, দুর্নীতিও বাড়ে। ভুয়া ট্রেজারি চালানও আছে প্রচুর, যার মাধ্যমে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; কিন্তু সত্যতা যাচাইয়ের উপায় নেই। এ জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করাই শ্রেয়। প্রযুক্তির সম্প্রসারণ হলে উদ্যোক্তারা কারখানায় বসেই অনলাইনে রিটার্ন ও অর্থ জমা দিতে পারবেন সহজে।
ভ্যাট ফাঁকি কোনো দেশে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে পেরেছে বলে জানা নেই। বাংলাদেশেও যে এটি রোধ করা যাবে, তা নয়। তবে এটি রোধ বা কর ফাঁকির প্রবণতা কমিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে খসড়া আইনের মাধ্যমে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ব্যবস্থা (Truncated base system) বিলুপ্ত করে দেয়া হচ্ছে। এটি আইনের বড় কাঠামোগত পরিবর্তন। এ ব্যবস্থা কার্যকর হলে ইনভয়েস চেইন পুরোটা বজায় রাখা সম্ভব হবে। আমদানি থেকে শুরু করে খুচরা বাজারে পণ্য বিক্রি পর্যন্ত ইনপুট ক্রেডিট চেইনও বলবৎ থাকবে। এখন আমদানিকারকরা ৩ শতাংশ ভ্যাট দিয়ে দিলে তাদের আর করব্যবস্থায় থাকার প্রয়োজন হয় না। ইনভয়েস চেইনটা কেটে যায় সেখানেই। এতে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা কী করলেন, সেটা জানতে পারছেন না রাজস্ব কর্মকর্তারা। সবাই মাঝে মধ্যে দুই বা তিন শতাংশ ভ্যাট দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। ইনপুট চেইন সিস্টেম চালু করা গেলে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা শুধু মার্জিনাল ভ্যালু এডিশনের ওপর ভ্যাট দেবেন। এখানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ডেভেলপ করবে। এ প্রক্রিয়াকে বলে ইনভয়েস সিস্টেমের ‘সেলফ পলিসিং’ (Self Policing) ম্যাকানিজম। এখানে করদাতারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করব্যবস্থা বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন কর চালান পত্রের মাধ্যমে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন এক লাখ টাকা পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমি কিছু উপাদান কিনলাম এবং তার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করলাম ১৫ হাজার টাকা। যার কাছ থেকে কিনলাম, তিনি বলতে পারেন, ভাই আপনাকে কম দাম লিখে দিই, আমি ভ্যাটটা কম দিই। আমি ভ্যাট ৭ হাজার ৫০০ টাকা লিখে দিই এবং দাম দেখাই ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কেন নেব, কারণ সে ক্ষেত্রে বাকি ৭ হাজার ৫০০ টাকা কে দেবে? পরবর্তী সময়ে আমি যখন ওই উপাদান ব্যবহার করে নতুন পণ্য প্রস্তুত করে দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করব, আমার ভ্যাট আসবে ২২ হাজার ৫০০ টাকা। এর থেকে আমি মাত্র ৭ হাজার ৫০০ টাকা বিয়োগ করতে পারব। কিন্তু যদি সঠিক ইনভয়েস নিতাম, তাহলে আমি ১৫ হাজার টাকা বিয়োগ করতে পারতাম। আমি ৭ হাজার ৫০০ টাকা ভ্যাট দিতাম, তাহলে ক্রেতা হিসেবে আমি কেন তাকে ভ্যাট ফাঁকিতে সহায়তা করব? বলব, না ভাই আমি যে মূল্যে কিনছি; তুমি সেই মূল্যই লিখে দাও। এ কারণে কর ফাঁকির সুযোগ কমে যাবে। করদাতা কাউকে খাতির করতে চাইলে নিজের ব্যয়ে তাকে সেটা করতে হবে। নতুন আইন বাস্তবায়ন হলে কেউই নিজের ক্ষতি করে অন্যকে সুবিধা দেবে না। আমার কোনো ক্ষতি না হলে অন্যকে খাতির করতে পারি তার অনুরোধে, যেটা বর্তমান কর ব্যবস্থায় হতে পারে। নতুন ব্যবস্থায় একজন আরেকজনকে পুলিশিং করবে, এ কারণে সারা বিশ্বে ইনভয়েস ব্যবস্থা এত সফল। এটি না হলে ভ্যাট আদায় বাড়বে না। কারণ এ ব্যবস্থাই হলো ভ্যাটব্যবস্থার মূল ভিত্তি।
দুর্বল করব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের কর-রাজস্ব জাতীয় আয়ের মাত্র ১০ দশমিক ৫ শতাংশ। এ অবস্থা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আইন ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন এ ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয়। বিভিন্ন দেশ, এমনকি প্রতিবেশি ভারতেও এটি সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হচ্ছে। জিডিপিতে কর সংগ্রহের হার ১২-১৩ থেকে ১৮-১৯ শতাংশে চলে এসেছে ভারতের। এটা হয়েছে মাত্র ৫-৭ বছরে। কর আইনের সংস্কার ও কর প্রশাসনে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটি সম্ভব করেছে ভারত সরকার। আমাদেরও কর আইন ও প্রশাসনে গুণগত এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনতে হবে। এ ধরনের পরিবর্তন আনতে পারলে, বিশেষত দুটি খাত মূল্য সংযোজন কর, যেটা ভোগের ওপর কর আর প্রত্যক্ষ কর, যেটা আয়ের ওপর কর— বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এ দুটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতই তখন উজ্জীবিত হবে। এতে সরকারের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাজস্ব আয় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ মুহূর্তে খসড়া ভ্যাট আইন পাস ও এর বাস্তবায়ন থেকে পিছিয়ে যাওয়া উচিত হবে না আমাদের।
লেখক: অর্থনীতিবিদ
নির্বাহী পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)






